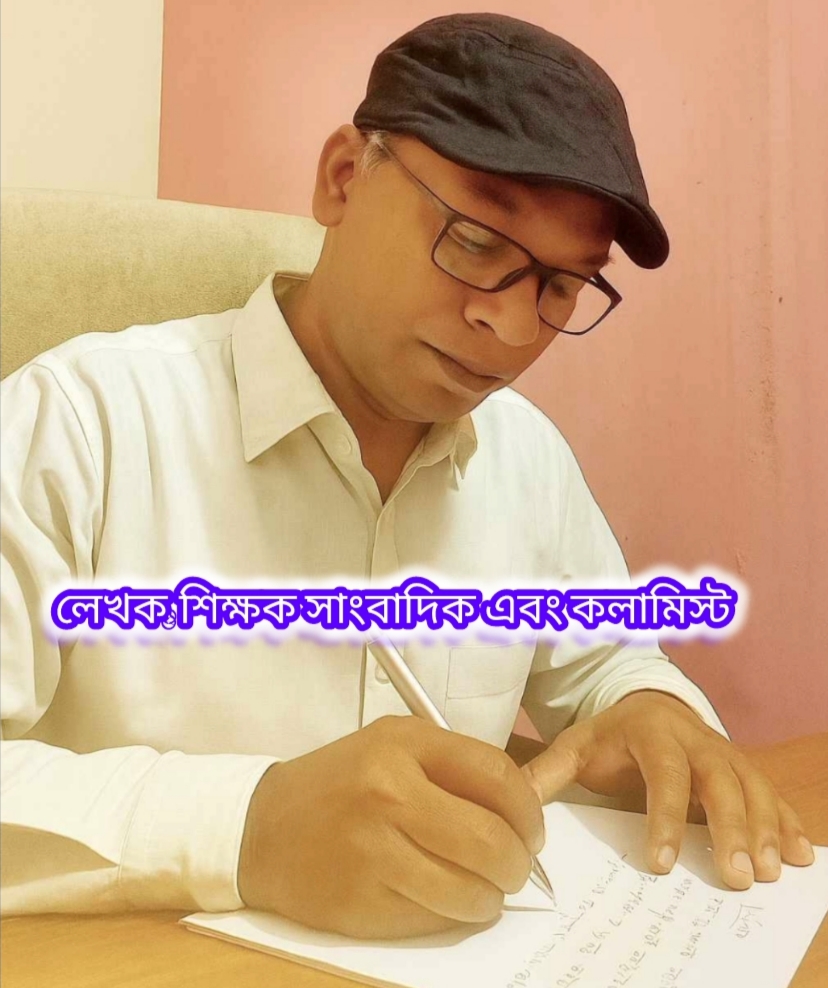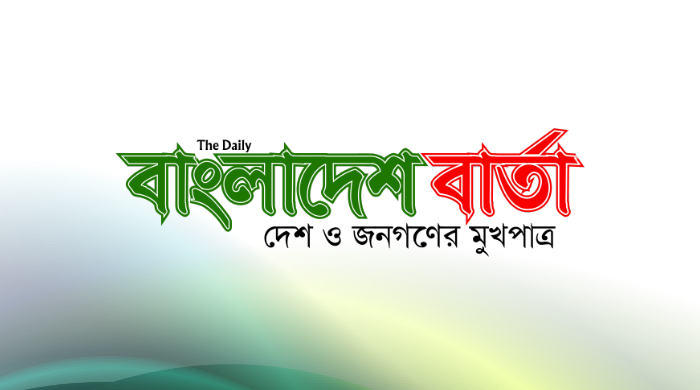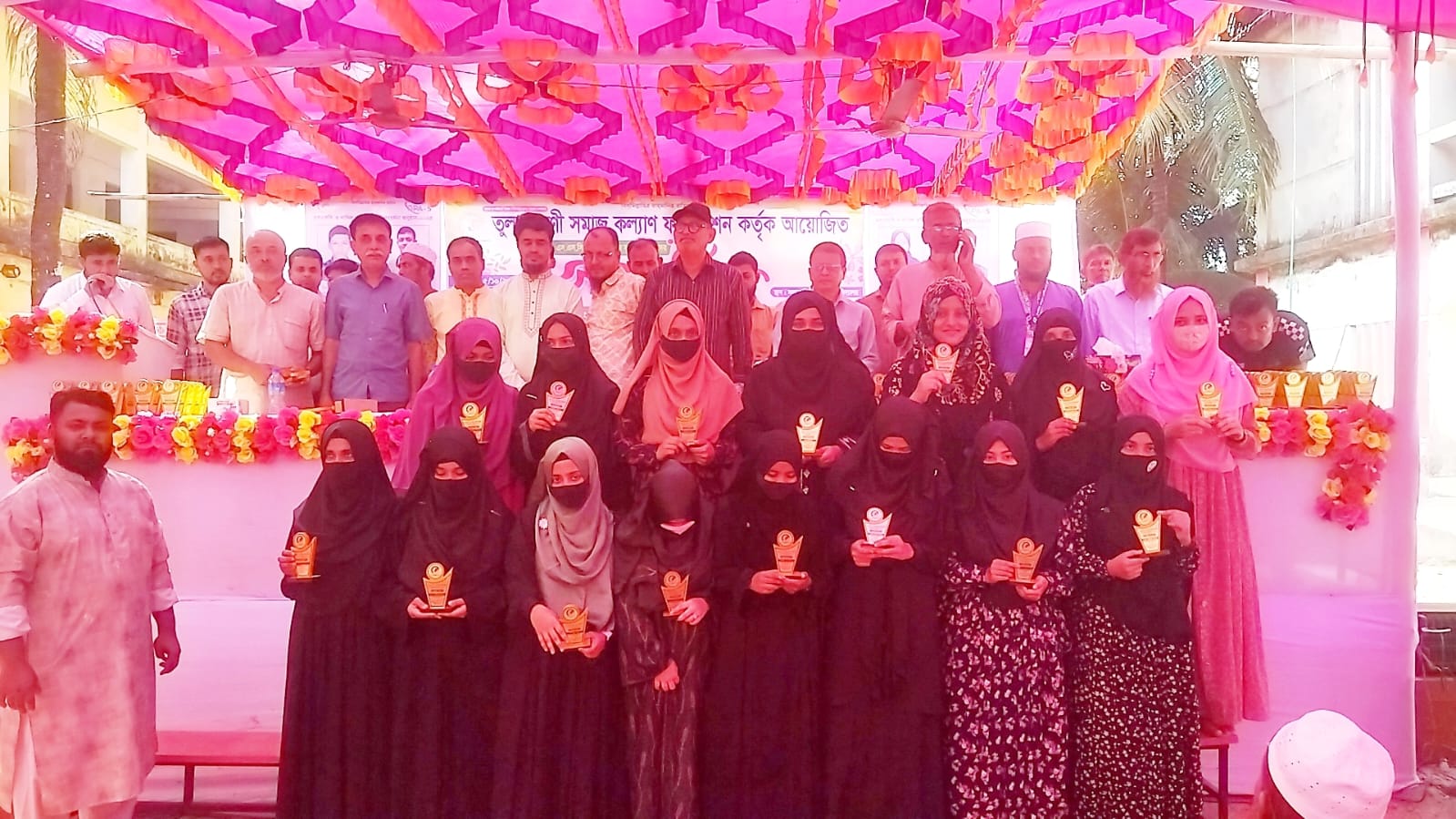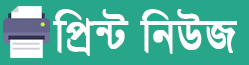
জিয়াউদ্দিন লিটন
বাংলাদেশে বিদ্যুৎ বিল নির্ধারণের ক্ষেত্রে বহুদিন ধরে চলমান একটি ব্যবস্থা হলো স্ল্যাব রেট সিস্টেম। এ ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট ইউনিট পর্যন্ত এক ধরনের হার প্রযোজ্য থাকে, এরপর সামান্য ব্যবহার বাড়লেই হঠাৎ করে উচ্চ হারে চার্জ আরোপ হয়। ফলে যে ভোক্তা ৭৯ ইউনিট বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন, তিনি একটি বিল দিচ্ছেন; অথচ মাত্র ১ ইউনিট বেশি ব্যবহার করায় ৮০ ইউনিটের ভোক্তা প্রায় দ্বিগুণ বিল পরিশোধে বাধ্য হচ্ছেন। এ বৈষম্যমূলক প্রথা ভোক্তাদের জন্য দীর্ঘদিনের ভোগান্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাস্তবতায় আজ এই পদ্ধতি বাতিল করে একক রেট চালু করা সময়ের দাবি হয়ে উঠেছে।
বিদ্যুতের ইতিহাস ঘেঁটে দেখা যায়, বারবার স্ল্যাব রেট পরিবর্তন ও দাম বৃদ্ধি ঘটেছে। ২০১২ সালের মার্চে প্রথম ১০০ ইউনিটে প্রতি ইউনিট ৩.০৫ টাকা, ১০০–৪০০ ইউনিটে ৪.২৯ টাকা এবং ৪০০ ইউনিটের বেশি হলে ৭.৮৯ টাকা হার চালু হয়। এতে গড়ে বিদ্যুৎ বিল প্রায় ৫০ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। তীব্র সমালোচনার মুখে একই বছরের সেপ্টেম্বরে স্ল্যাবভিত্তিক বিলিং বাতিল করে প্রতি ইউনিট ৫.৭৫ টাকার গড় হার নির্ধারণ করা হয়। এরপর ২০১৪ সালের মার্চে আবার গড়ে ৬.১% থেকে ৯.৯৪% পর্যন্ত বিদ্যুৎ মূল্য বাড়ানো হয়। ২০২০ সালের মার্চে খুচরা রেট ৬.৭৭ টাকা থেকে বেড়ে ৭.১৩ টাকা হয়, যা প্রায় ৫.৩% বৃদ্ধি। ২০২৪ সালের ফেব্রুয়ারিতে আবারও খুচরা রেট বেড়ে ৮.২৫ টাকা থেকে ৮.৯৫ টাকা হয় এবং একইসঙ্গে lifeline ভোক্তাদের হারও ৪.৩৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৪.৬৩ টাকা করা হয়। সর্বশেষ ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে সরকার ঘোষণা দিয়েছে—বিদ্যুতের খুচরা দাম আর বাড়ানো হবে না; বরং উৎপাদন খরচ ১০ শতাংশ কমানো হবে।
এত বছরের পরিসংখ্যান প্রমাণ করে, বিদ্যুতের দাম ধাপে ধাপে বাড়লেও স্ল্যাব রেট ব্যবস্থা বরাবরই ভোক্তার ওপর অতিরিক্ত চাপ সৃষ্টি করেছে। এই ব্যবস্থার সমস্যা বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি বিষয় পরিষ্কার হয়ে ওঠে। প্রথমত, এটি ভোক্তাদের মনে অযথা আতঙ্ক তৈরি করে। মানুষ বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে গিয়ে সবসময় চিন্তায় থাকে—এক ইউনিট বাড়লেই বিল হঠাৎ বেড়ে যাবে। দ্বিতীয়ত, এতে রয়েছে স্পষ্ট বৈষম্য। সমান ব্যবহারের ক্ষেত্রে একজনকে কেবল সামান্য বেশি ইউনিট খরচ করায় অতিরিক্ত অর্থ দিতে হয়। বিদ্যুৎ যেহেতু একটি মৌলিক সেবা, তাই এটিকে কোনোভাবেই শাস্তিমূলক নীতিতে বেঁধে রাখা যায় না। তৃতীয়ত, এই বিলিং প্রক্রিয়া জটিল ও অস্বচ্ছ। সাধারণ ভোক্তা বুঝতেই পারেন না কোন ইউনিটে কত টাকা হিসাব করা হয়েছে। ফলে আস্থাহীনতা তৈরি হয়।
সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন নিম্নআয়ের মানুষ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি। তারা সামান্য অতিরিক্ত ব্যবহার করলেও অপ্রত্যাশিত বিলের ধাক্কা সামলাতে হয়। অন্যদিকে শিল্পপ্রতিষ্ঠান তুলনামূলকভাবে পরিকল্পিত হারে বিদ্যুৎ ব্যবহার করতে পারে। এতে সামাজিক বৈষম্য আরও প্রকট হয়। বিদ্যুৎ ব্যবহারে সাশ্রয়ী মানসিকতা তৈরি হওয়ার বদলে মানুষের মনে আতঙ্ক ও অবিশ্বাস জন্ম নেয়।
তবে আশার কথা হলো, সরকার ইতোমধ্যেই উৎপাদন খরচ ১০ শতাংশ কমানোর পরিকল্পনা নিয়েছে। এই উদ্যোগ একক রেট কার্যকরে সহায়ক হতে পারে। রাজস্ব ঘাটতির ঝুঁকিও থাকবে না; বরং বিল আদায়ে স্বচ্ছতা নিশ্চিত হবে। জনগণ সহজেই নিজের ব্যবহার হিসাব করতে পারবেন এবং বিদ্যুৎ ব্যবস্থার প্রতি আস্থা ফিরে আসবে।
বিদ্যুৎ বিল একক রেটে নির্ধারণ করা হলে প্রতিটি ভোক্তা সমান হারে চার্জ দেবেন। এতে বৈষম্য দূর হবে, বিভ্রান্তি কমবে এবং জনগণের আস্থা বাড়বে। বিশ্বের অনেক দেশেই একক রেট বিলিং চালু রয়েছে। বাংলাদেশেও এটি এখন সম্ভব, কারণ দেশে ব্যাপকভাবে ডিজিটাল ও প্রিপেইড মিটার চালু হয়েছে।
২০১২ সালে প্রথম ১০০ ইউনিটে ৩.০৫ টাকা থেকে শুরু করে ২০২৪ সালে ৮.৯৫ টাকা পর্যন্ত বিদ্যুতের দাম বৃদ্ধি প্রমাণ করে—স্ল্যাব রেট ভোক্তাদের বিভ্রান্তি আর বাড়তি বোঝা ছাড়া কিছুই দেয়নি। সর্বশেষ বাজেটে দাম না বাড়ানোর ঘোষণা ইতিবাচক হলেও ভোক্তাবান্ধব বিদ্যুৎ ব্যবস্থার জন্য সবচেয়ে জরুরি কাজ হলো স্ল্যাব রেট বাতিল করে একক রেট চালু করা। এতে বিদ্যুৎ বিল হবে ন্যায়সঙ্গত, স্বচ্ছ ও আধুনিক বাংলাদেশের জন্য উপযোগী। একইসঙ্গে দেশের অর্থনৈতিক শৃঙ্খলা ও জ্বালানি নীতির স্থিতিশীলতার জন্যও এটি হবে সময়োপযোগী ও জনগণকেন্দ্রিক পদক্ষেপ।
লেখক: শিক্ষক সাংবাদিক এবং কলামিস্ট।
(জিয়াউদ্দিন লিটন)

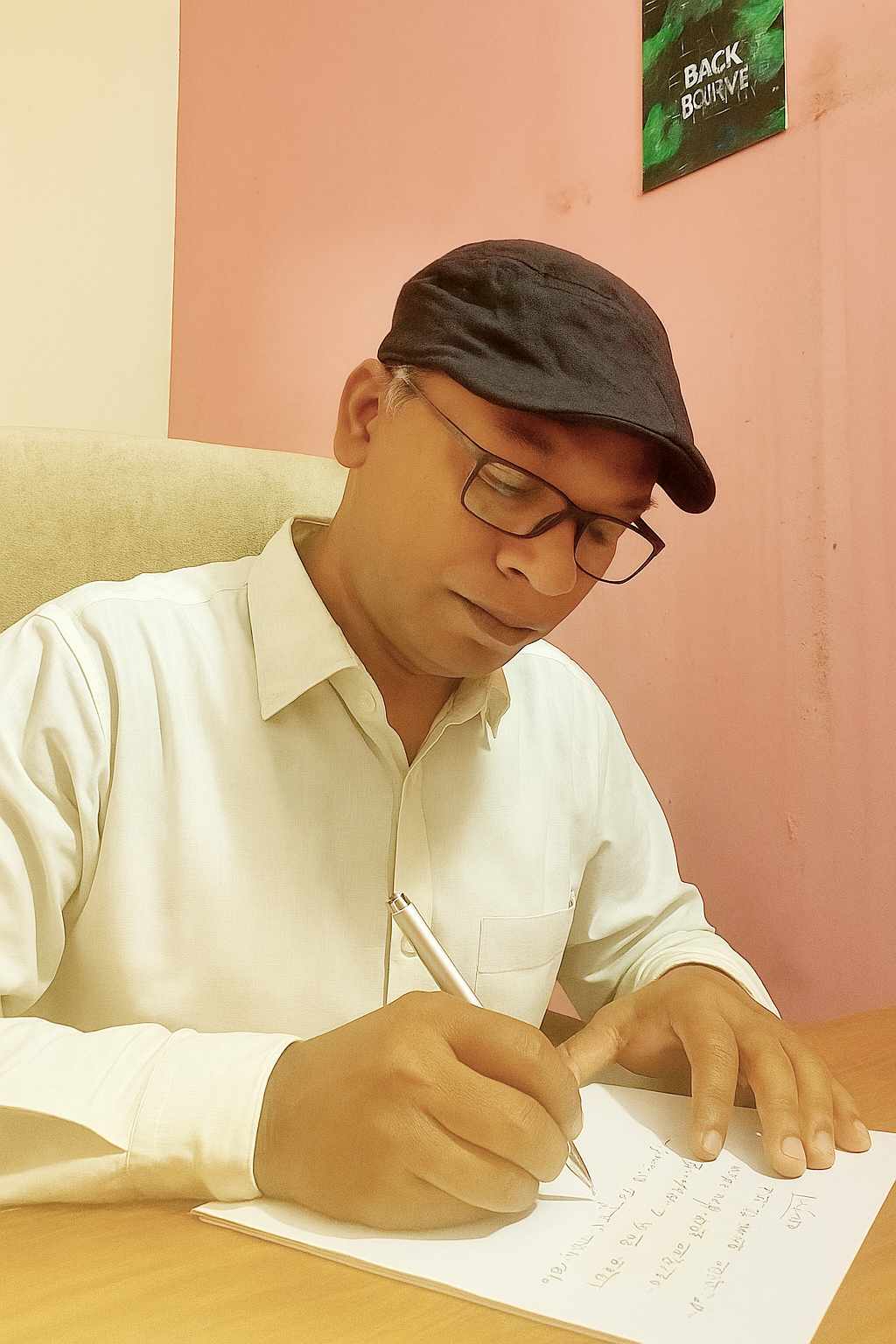 জিয়াউদ্দিন লিটনঃ
জিয়াউদ্দিন লিটনঃ